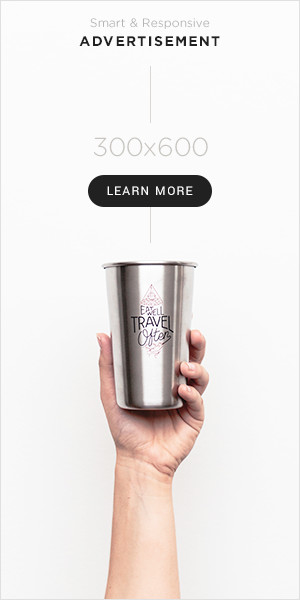এ. এইচ. এম. ফারুক:
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু দিন যাবৎ উপজাতিদের সঠিক পরিচিতি নিয়ে নানান প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। একটি বিশেষ মহল বারবার বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে পরিস্থিতিকে বেসামাল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের নিয়েই এ প্রপাগান্ডা চলে বেশি। ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বসবাস করছে। আর তা কোনভাবেই ৪শ’ বছরের বেশী নয়। বাংলাদেশে তারা অভিবাসী।
ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রানুযায়ী, তারা বাংলাদেশের আদিবাসী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে দাবী করছে। অপরদিকে আদিবাসীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না মর্মে জাতিসংঘের সাথে পশ্চিমারা সম্প্রতি খুব হৈ চৈ শুরু করেছে। মজার বিষয় হচ্ছে, জাতিসংঘের যেসব সদস্য দেশে আদিবাসী রয়েছে, তাদের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই । অন্যদিকে, জাতিসংঘ পশ্চিমাদের বিশেষ কূট-কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাদামী এবং কালো চামড়ার দেশগুলোর ওপর নৈতিকতার দোহাই দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কনভেনশন ১৬৯ চাপিয়ে দিতে চাইছে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এই সনদে স্বাক্ষর করার চাপ দিচ্ছেন। তাই ইতিহাসভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসী অভিধাযোগ্য কোন জনগোষ্ঠী আছে কিনা, তা পর্যালোচনা করা অতি জরুরীভাবে দরকার। নিম্নে এ পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:
বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত, সেগুলো হলো : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মগ, কুকি, লুসাই, সেন্দুজ, পাংখো, বনযোগী, খুমি, গারো, হাজং, মণিপুরী, পাঙ্গন, খাসিয়া, সাঁওতাল, ওরাও, রাজবংশী প্রভৃতি ২৯টি জনগোষ্ঠী। এসব জনগোষ্ঠীতে ধর্মীয় দিক থেকে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান এমনকি ইসলাম ধর্য়ের অনুসারীও রয়েছে (মৌলভীবাজার জেলায় প্রায় ৩০ হাজার মুনিপুরী/পাঙ্গন ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী মুসলীম ধর্মাবলম্বী)। তারা রাষ্ট্রের সাধারণ মানবমণ্ডলী তথা নাগরিকমণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাদের কল্যাণে ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে অন্যান্য নাগরিকের মতোই। এখানে এ মুহূর্তে যে বিষয়টা গুরুত্ববহ সেটা হলো, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুসারে উপরে বর্ণিত জনগোষ্ঠীগুলোকে ভূমিজ সন্তান বলা যায় কিনা? এসব উপজাতিদের নিজস্ব যে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা অদূর অতীতে বাংলাদেশের সীমানার বাইরে অপরাপর রাজ্য কিম্বা অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক কারণে এবং বিশেষ করে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা সবাই কোন না কোন ধর্মানুসারী ছিল, সভ্য জীবনযাপন করত, রাজ্যশাসন করত, প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে হেরে বাংলাদেশের কোন না কোন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য। স্বীকৃত সব নৃ-তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এরা কোনভাবেই, কোন সংজ্ঞায় ‘আদিবাসী’ হিসেবে অভিহিত হতে পারে না।
আদিবাসী বলতে কী বোঝায়
ইংরেজী Indigenous শব্দটির বাংলা হচ্ছে আদিবাসী। “A person or living thing that has existed in a country or continent since the earliest time known to people ” . অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কোন এলাকার বিশেষ জনগোষ্ঠী যদি ঐ এলাকায় বসবাস করে তাহলে তাদেরকে ঐ এলাকার আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। Indigenous শব্দটির অর্থ হচ্ছে Nation born originating or produced naturally in a country, not imported. অর্থাৎ আদিবাসী হতে হলে অভিবাসী হলে হবে না, বরং সত্যিকারভাবে একটি দেশে প্রাচীনকাল থেকে উৎপত্তি হতে হবে। এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ লুইজ মর্গান আদিবাসীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, “The Aboriginals are the groups of human race who have been residing in a place from time immemorial – They are the Sons of the soilÓ. আদিবাসী হতে হলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য থাকতে হবে যা হলো “ভূমিপুত্র” বা Ò Sons of the soilÓ. জাতিসংঘ থেকে UNPFII (United Nation Permanent Forum for Indigenous Issues)- এর মাধ্যমে কারা আদিবাসী হবে তার একটি মানদন্ড ঠিক করা হয়েছে। জাতিসংঘ কমিশনের স্পেশাল র্যাপটিয়ার হোসে মার্টিনেজ কোবে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, “কোনভূখন্ডের আদিবাসী সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী বা জাতি বলতে তাদের বোঝায়, যাদের ঐভূখণ্ডে প্রাক-আগ্রাসন এবং প্রাক-উপনিবেশকাল থেকে বিকশিত সামাজিক ধারাসহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ঐ ভূখণ্ডে বা ভূখণ্ডের কিয়দাংশে বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। সেই সাথে তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পূর্বপুরুষের ভূখণ্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ”। জাতিসংঘের সংজ্ঞায় মূলত তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যা হলো : ১. যারা কোন উপনিবেশ স্থাপনের আগে থেকেই ওই ভূখণ্ডে বাস করছিল, ২. যারা ভূখণ্ডের নিজস্ব জাতিসত্ত্বার সংস্কৃতি ধরে রেখেছে এবং তা ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ৩. যারা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে। এই সংজ্ঞাসমূহের আওতায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষকগণ সত্যিকার অর্থে কারা আদিবাসী তার উদাহরণ দিতে যেয়ে বলেছেন যে, খর্বাকৃতি, স্ফীত চ্যাপ্টা নাক, কুঁকড়ানো কেশবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের ‘বুমেরাংম্যান’রা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বা যথার্থ অ্যাবোরিজিন্যালস। তারা ওখানকার ভূমিপুত্র বটে। ঠিক একইভাবে মাউরি নামের সংখ্যালঘু পশ্চাৎপদ প্রকৃতিপুজারি নিউজিল্যান্ডের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সেখানকার আদিবাসী। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এসব সংজ্ঞার অন্তর্ভূত নয়। তারা বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে চট্টগ্রাম তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে ১৭শ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮শ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের দিকে।
উপরোক্ত সূত্রের আলোকে অবশ্যই বলা যায়, একমাত্র বাঙালিরাই এই এলাকার আদিবাসী, যারা ব্রিটিশ কলোনী স্থাপনের আগে তো বটেই, সেই প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, স্বতন্ত্র, সামাজিকতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত স্বতন্ত্রবোধ বজায় রেখেছে। সে হিসেবে বাঙালিরাই এখানকার একমাত্র ‘ভূমিপুত্র’। এখানে আরেকটা কথা উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশরা সেটেলমেন্ট কলোনাইজেশন না করায় এ অঞ্চলের আদিবাসিন্দা বাঙালিদের কখনই মূল ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনাতো দূরের কথা, এমনকি বাঙালিদের ভাষা, কৃষ্টি, কালচার এর উপরও কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। সুতরাং এই বিবেচনায়ও বাঙালিরাই এই এলাকার প্রাচীনতম ও একমাত্র আদিবাসী। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশের সমতলে কিংবা পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর পরিচয় তাহলে কী হবে ? আদিবাসীর সংজ্ঞা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে এটাই বোঝা যায় যে, সমতলে কিংবা পাহাড়ে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগুলো বহিরাগত এবং তারা অভিবাসী জনগোষ্ঠী, কোনো কোনো গোষ্ঠীকে উপজাতি বলা যায়। তবে কোন ভাবেই আদিবাসী নয়।
পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতির সূত্রপাত এবং যে কারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো আদিবাসী নয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃহত্তর চট্টগ্রামেরই অংশ। প্রশাসনিক কারণে ইংরেজ শাসানমলে চট্টগ্রামের পূর্বের অরণ্য এলাকাটি পৃথক করে এর নামকরণ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। পৃথক হবার পূর্বে থেকে সমগ্র চট্টগ্রাম জুড়েই চট্টগ্রামীরা বসবাস করে আসছে। এমনকি মোগল শাসনামলে সীমান্ত পাহারায় রাঙ্গামাটিতেও একটি সামরিক দূর্গ ছিল। এই দূর্গকে কেন্দ্র করে আশে-পাশে বিপুল সংখ্যক চট্টগ্রামী বসবাস করতো। সে বিষয়ে মোগল শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তে স্পষ্টই জানা যায়। চট্টগ্রামীরা বনজসম্পদ আহরণে অরণ্যে যাতায়াত করতো এবং কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী কোন কোন এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যও গড়ে তুলেছিলো। এমনই সময় অর্থাৎ ১৬শ’ খ্রিস্টাব্দের দিকে উত্তরাংশে অর্থাৎ আজকের খাগড়াছড়ি এলাকায় কিছুসংখ্যক ত্রিপুরা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এসে গহীন অরণ্যে জুম চাষাবাদ শুরু করে। এছাড়া আসামের মিজোরামের অরণ্য থেকে কুকি নামক এক উলঙ্গ জাতিও মাঝে মধ্যে বিচরণ করত চট্টগ্রামের এই অরণ্য পথে। তারা কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরে-ফিরে আবার চলে যেত মিজোরামে।
স্থানীয় ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসবিদ ও জাতীয় পর্যায়ের ইতিহাসবিদগণের লিখিত ইতিহাস অনুযায়ী দেখা যায়, ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আরাকান থেকে বিতাড়িত একদল চাকমা সর্বপ্রথম নাফ নদী পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের রামু থানার অদূরে নদী তীরে অবস্থান নেয়। তারা সেখানে সল্প সময় অবস্থানের পর গভীর অরণ্যে (বর্তমান আলীকদম উপজেলা) চলে যায়। চাকমারা কেন রামু থেকে আলীকদম এবং আলীকদম থেকে রাঙ্গামাটির দিকে এলো তার একটা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক তাৎপর্যও পাওয়া যায়। তা হল: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহ সুজা আপনভাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে চট্টগ্রামের প্রাচীন বন্দর শহর দেয়াঙ-এ (বর্তমানে আনোয়ারা উপজেলা) আশ্রয় নেয়। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর অনুগত ১৮ জন সেনাপতির নেতৃতে সেনাবাহিনীকে রামুতে রেখে শুধু তাঁর নিকটাত্মীয়দের নিয়ে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে আরাকানের রাজধানীতে যান। উল্লেখ্য যে, প্রায় একই সময়ে আরাকান থেকে বিতাড়িত চাকমাদের প্রথম দলটি রামুর নদী তীরে (চাকমারকুল) অবস্থান নিয়েছিল। সে সময়ে মোগল সৈনিকদের সাথে চাকমা শরণার্থীদের যোগাযোগ ঘটে। এদিকে আরাকানের রাজধানীতে আশ্রয়ের কিছু সময়ের মধ্যে আরাকানের তৎকালীন তরুণ রাজা সুবেদার শাহ সুজার এক কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সুজা তাতে ক্ষুদ্ধ হয়ে আরাকানের রাজার সাথে বাকবিতন্ডা ও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে আরাকানের রাজার হাতে সপরিবারের নিহত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামুতে অবস্থানরত মোগল যোদ্ধাদের সাথে আরাকানী সৈনিকদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং মোগল যোদ্ধারা রামু ত্যাগ করে পূর্বে গভীর অরণ্যে গিয়ে পুনরায় দূর্গ স্থাপন করে। মোগল যোদ্ধারা ইসলামের অন্যতম খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুসারী শিয়া সম্প্রদায়ের হওয়ায় তারা হযরত আলীর নামানুসারে ঐ এলাকার নামকরণ করেন ‘আলীকদম’ (বর্তমানে আলীকদম উপজেলা)। মোগলযোদ্ধাদের পিছু পিছু চাকমারকুলের চাকমারাও চলে যায় আলীকদমে। মূলত এখানেই নারী বিহিন মোগল যোদ্ধাদের সাথে চাকমাদের এমন এক সমাজ গড়ে ওঠে যাতে বহু মোগলযোদ্ধা চাকমা রমণী বিয়ে করে সংসার জীবনও শুরু করে।
এদিকে সহোদর শাহ সুজা হত্যাকাণ্ডে ক্ষুদ্ধ হয়ে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেনাপতি শায়েন্তা খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে বাংলায় পদার্পন করেন। ১৬৬৬ সালের প্রথম দিকে শায়েস্তা খাঁ আপন পুত্র উমেদ খাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে আরাকানের অভিযানের নির্দেশ দেন। ২৭ জানুয়ারী ১৬৬৬ তারিখে মোগলরা ব্যাপক হতাহতের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রাম বিজয় করে নেয়। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর প্রধান সেনাপতি উমেদ খাঁ চট্টগ্রামের নবাব হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন এবং আলীকদমে আশ্রিত মোগলদের মাধ্যমে কার্পাস-কর প্রদানের শর্তে আলীকদমে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ জমিদারীর প্রজা হয় বার্মা থেকে বিতাড়িত সেই জুমিয়া চাকমারা। এভাবেই চলছিল কয়েক বছর। পরবর্তীতে মোগল ও আরাকানীদের অব্যাহত খন্ড খন্ড যুদ্ধের কারণে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল ঐ সময় ‘নো-ম্যান্সল্যান্ড’ নামে অভিহিত হয়। ঐ এলাকা চট্টগ্রামের নবাবের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও সেখানকার জমিদার শের জালাল খাঁ নিকটবর্তী আরাকানীদের বারংবার হামলার কারণে আরাকানীদের সাথে মিত্রতা ও তাদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং চট্টগ্রামের তৎকালীন নবাব মীরহাদীকে কর না দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এতে চট্টগ্রামের নবাব ক্ষুদ্ধ হয়ে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে জমিদার জালাল খাঁ’র প্রাসাদ ও যাবতীয় স্থাপনা ধ্বংস করে দেন। সেই সাথে জুমিয়া চাকমাদের উপরও হামলা চালিয়ে তাদের সবকিছু ধ্বংস করে দেন। ফলে অনন্যোপায় জালাল খাঁ আরাকানের অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন। সেখানেও তিনি আরাকানীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। জুমিয়া চাকমারাও প্রাণ রক্ষার্থে নানাস্থানে আশ্রয় নেয়। সে সময় চট্টগ্রামের দেয়াঙে (আনোয়ারায় থানা) বসবাসরত জালাল খাঁ’র সহযোদ্ধা সেনাপতি শেরমস্ত খাঁ’র ছিল বিশাল প্রতিপত্তি যিনি ক্রমান্ময়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণে চকরিয়া-রামু পর্যন্ত বিস্তীর্ণভূমির জমিদারী লাভ করেছিলেন। আলীকদম ট্রাজেডির ১৩ বছর পর ঐ শেরমস্ত খাঁ-ই মোগল নবাব জুলকদর খানের কাছ থেকে রাঙ্গুনীয়ার কোদালা-পদুয়া এলাকা (বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলার একাংশ) বন্দোবস্তি এবং পার্বত্য অঞ্চলের জুমকর আদায়ের তহশিলদারী লাভ করেন । সেখানে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত আলীকদম থেকে সহযোদ্ধা মোগল সৈনিক ও তাদের পরিবার পরিজন এবং জুমিয়া চাকমা প্রজাদেরকে নিয়ে এসে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। উদ্বাস্তু এসব চাকমারা শেরমস্ত খাঁর খামার আবাদে নিয়োজিত হয়। উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে শেরমস্ত খাঁর অনুসারী হয়ে কোদালা, পদুয়ায় আগত চাকমারা অনেকে মোগলদের ধর্ম গ্রহণ করে।
১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব মীর কাসিম ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট চট্টগ্রামের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ প্রশাসকগণ রাঙ্গুনীয়ার কোদালা-পদুয়া থেকে অনতিদূরে সাংগু নদী এবং সীতাকুন্ডের নিজামপুর রোড পর্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে পদুয়া-কোদালার জমিদারির সীমানা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন যার দায়িত্বে ছিলেন শেরমস্ত খাঁর উত্তরসরী শের জব্বার খাঁ । তিনি মোগল শাসামলের নিয়মেই ইংরেজদের কর প্রদান করতে থাকেন এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কর প্রদান করেছিলেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা বোধপায়া ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নাফ নদীর তীরবর্তী আরাকানরাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নেয়। বর্মী সৈন্যদের নৃশংস গণহত্যা ও নির্যাতনের ফলে প্রাণ রক্ষার্থে হাজার হাজার মারমা, চাকমা ও অন্যন্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নাফ নদী পাড়ি দিয়ে কক্সবাজার আশ্রয় গ্রহণ করলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এসব শরণার্থীদের কর প্রদানের শর্তে পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষের সুযোগ করে দেয়। আরাকান থেকে দ্বিতীয় দফায় আগত এ জনগোষ্ঠী চট্টগ্রামের অরণ্যে প্রবেশ করে চলে আসে পদুয়া-কোদালায় এবং পূর্বে আগত গোষ্ঠীগদ চাকমাদের সাথে সহজেই মিশে যায়। ফলে এসব জুমিয়া চাকমা ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জমিদারে উপর করও বাড়িয়ে দেয়। তৎকালীন জমিদার জানবক্স খাঁ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেন এবং কর প্রদান বন্ধ করে দেয়। তাতে সরকার তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালালে তিনি কলিকাতায় গিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন এবং পুনরায় জমিদারি পরিচালায় চুক্তিবদ্ধ হন। পুনরায় যাতে বিদ্রোহ না হয় সে জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে উত্তর রাঙ্গুনীয়ার সমতলভূমিতে জমিদারি কাচারি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে, তারই জমিদারবাড়ির নামানুসারে ঐ এলাকার নামকরণ হয়ে যায় রাজানগর।
রাজানগরে মোগল বংশজাত সর্বশেষ জমিদার বা চাকমাদের রাজা ছিলেন ধরমবক্স খাঁ। তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন চাকমা রমণী কালিন্দীর সাথে এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারীর উত্তরাধিকার নিয়ে তারই স্বগোত্রীয় মীর্জা হোসেন খাঁর সাথে রাণী কালিন্দীর দ্বিমত দেখা দেয়। একদিকে মীর্জা হোসেন খাঁর নেতৃত্বে মোগল বংশজাত মুসলিমরা অন্যদিকে রাণী কালিন্দীর নেতৃত্বে চাকমা জুমিয়ারা। অপরদিকে বার্মা থেকে বিতাড়িত প্রায় ৪ হাজার বিদ্রোহী তঞ্চঙ্গ্যা রাণী কালিন্দীর সাথে যোগ দিয়ে চাকমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে। ফলে এসব বাঙালি তথা মোগল পরিবারগুলো প্রাণভয়ে সমতলের দিকে ছুটে যায় এবং পার্বত্য জমিদারী পরিচালনায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আদালত ধরমবক্স খাঁর স্ত্রী হিসেবে রাণী কালিন্দীর পক্ষে রায় ঘোষণা করে। সেই সাথে রানী কালিন্দীর খড়গতলে শত বছরের মোগল জমিদারী মুসলিম পরিবারের হাতছাড়া হয়ে যায়। রাণী কালিন্দী তাঁর জমিদারীকালে মোগল ঐতিহ্য দেওয়ান পদবি বাতিল করে তদস্থলে তালুকদার নামক একটি নতুন পদ চালু করেন। তাঁর উত্তরসূরী হরিশচন্দ্র পূনরায় মোগলদের সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়লে আদালত মোগলদের পক্ষে রায় দেয় (উল্লেখ্য যে, বেশ কটি মোগল পরিবার আজও রাঙ্গুনীয়ায় বসবাস করে আসছে)। এতে হরিশচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গুনীয়ার রাজানগর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নতুনভাবে বসবাস স্থাপন করেছিলেন রাঙ্গামাটিতে। এভাবেই ১৭শ-১৮শ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক চাকমা, মারমা এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত হয়ে যায়।
পূর্ববর্তী আলোচনায় নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, পাহাড়ের বর্তমান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো হল অভিবাসী। সুতরাং তারা চট্টগ্রাম তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘ভূমিপুত্র’ না হওয়ায় আদিবাসী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।
বহিরাগত হওয়ার কারণে ইংরেজ সরকার তাদেরকে নিজ শাসনাধীন মনে করতেন না। চট্টগ্রামের কমিশনার মি. হলহেড ১৮২৯ সালে মন্তব্য করেন যে, `The hill tribes are not British subjects but merely tributaries and that we recognized no right on our part to interfere with their internal arrangement’. ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলকে নন-রেগুলেটড এরিয়া বা অশাসিত-এলাকা হিসেবে উল্লেখ করে এবং ১৯২০ সালে এলাকাটিকে Exclusive Area- হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার এলাকাটিকে একান্ত Exclusive Area-এর পরিবর্তে উপজাতি এলাকা হিসেবে অভিহিত করে। যদি ১৯০০ সাল থেকেও ধরি তাহলে দেখা যাবে কোথাও কোন পর্যায়ে এ এলাকাকে আদিবাসী এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে যে শান্তিচুক্তি সারিত হয়েছে তাতেও স্থান পায়নি আদিবাসী শব্দটি। এমনকি এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো তাদের অধিকার আদায়ের দীর্ঘ বছরের সংগ্রামেও নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ করেছে এমন প্রমাণ কোথাও নেই। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কনভেনশন ১০৭ (যা বাংলাদেশ সাক্ষর করেছে) অনুসারেও এ এলাকায় কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী থাকলে তারা একমাত্র চাঁটগাইয়া বাঙালিরা (চট্টগ্রামের বাঙালি) ছাড়া আর কেউ নয়।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী বানাতে আন্তর্জাতিক মহল উদগ্রীব
নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিরিখে জাতিসংঘের আদিবাসী ফোরামের দেয়া মানদন্ড অনুসারে যারা আদিবাসী হওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরই আবার আদিবাসী হওয়ার স্বীকৃতির বিষয়টি আধিপত্যবাদের নতুন কোন ফন্দি ফিকির ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত পশ্চিমারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী হীন ও নীচ চিন্তা-ভাবনা থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিজস্ব রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদিবাসী ইস্যু সৃষ্টি করছে যা পাহাড়ী বাঙালি কারও জন্যেই মঙ্গলকর কিছু আনবে না, বরং জন্ম দিতে পারে নৃশংস দাঙ্গা-হাঙ্গমা ও বিভাজনের।
সবাই বাংলা মায়ের সন্তান
ইতিহাসের সততার স্বার্থে কোন প্রকার ধূম্রজাল সৃষ্টি হতে দেয়া উচিৎ নয়। যা সত্য, সহজভাবে তার ছায়াতলে দণ্ডায়মান হলে অনেক প্রকার সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। বর্ণিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগনের পূর্বপুরুষেরা প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ থেকে এলেও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ মুহূর্তে বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগনের জন্ম বাংলাদেশে, তাদের জীবনযাপন বাংলাদেশে এবং সর্বাগ্রে তারা বাংলাদেশের সন্তান। তারা বাংলাদেশেরই নাগরিক এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অপরাপর কোন জনগোষ্ঠীও বিন্দুমাত্র দ্বিমত পোষণ করে না। আন্তর্জাতিক কুটিল রাজনীতির পর্দা সরিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাকালে দেখা যায়, এ এলাকার শ্রমজীবী জনতা তথা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা এবং বাঙালি জনগণ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু ও মুসলিম যাই হোক না কেন পরস্পর পরস্পরের জীবন সংগ্রামের সহযোদ্ধা। সবাই সবার ভাই এবং সবারই অধিকার সমান। এটাই হচ্ছে সত্যিকারের বাস্তবতা। সুতরাং, আমরা আমাদের সার্বভৌমত্বকে বলি দিয়ে নতুন কোন দক্ষিণ-সুদান কিংবা পূর্ব-তীমূর সৃষ্টি করতে পারি না। আমাদের উচিৎ বহিঃশত্রুর কুমন্ত্রণায় কান না দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থে এক ছাতার নিচে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন সংগ্রামের পথ পাড়ি দেয়া। সঠিক ইতিহাসকে আমলে নিয়ে “সবার উপরে দেশ” এ মূল-মন্ত্রকে শীরধার্য করে আসুন আমরা আগামী প্রজন্মকে একটি নিষ্কণ্টক ভবিষ্যৎ উপহার দিয়ে যাই।
এ. এইচ.এম ফারুক- নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক মানবাধিকার খবর।