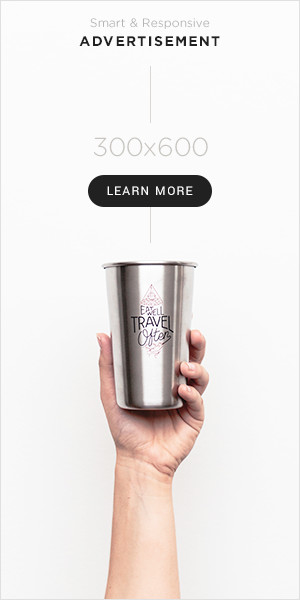শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহ আন্তঃকলহ, বিভাজন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, নেতৃত্বের সংকট, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সর্বোপরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে পার্বত্য জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি তাদের আন্দোলন-কর্মসূচি জনবিমুখ ও স্থবির হয়ে পড়েছে।
বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএস (মূল), ইউপিডিএফ এবং নব্যসৃষ্ট জেএসএস (সংস্কারপন্থী) দল ও তাদের অঙ্গ-সংগঠনসমূহ সক্রিয় থাকলেও তাদের কার্যক্রম মূলত আন্তঃদলীয় কোন্দল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ। নিকট অতীতে এসকল দলসমূহ শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, ভূমি সমস্যার সমাধান, উপজাতীয় উদ্বাস্তু শরণার্থী পুনর্বাসন, বাঙালিদের সমতলে স্থানান্তর, সেনাক্যাম্প অপসারণসহ স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও সাধারণ উপজাতির অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। পার্বত্য সমস্যার সূচনাকাল হতে এসকল রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশীয় নেতৃত্ব, সংস্থা ও সংগঠন সাহায্য, সমর্থন, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এসেছে।
সম্প্রতি আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় কিছু সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আঞ্চলিক দলসমূহ ‘আদিবাসী’ ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। এরই অংশ হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিমণ্ডলে একতরফাভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় বাংলাদেশের পার্বত্য জেলায় বসবাসরত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসাবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। এ কাজে আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থা, এনজিও এবং দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আর্দশগত ও মতের মিল না থাকলেও অন্তত এই একটি বিষয়ে আঞ্চলিক দলসমূহ একটি মতানৈক্যে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা যায়।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠীকে নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় সংসদে বিল পাশ করা হলেও সাম্প্রতিককালে ‘আদিবাসী’ নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার অসাংবিধানিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ‘স্বকীয়তা’ সুরক্ষার নামে নতুন করে তাদের মুখের ভাষার জন্য ইংরেজীতে বর্ণমালা তৈরি বা ‘লৈখিক ভাষা’ সৃষ্টিরও প্রয়াস চলছে। এক্ষেত্রে কিছু বিদেশী সংস্থার উদার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্যণীয়। এসকল কর্মকাণ্ড এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথক করে রাখার কোনো দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ কিনা, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা ভালো কাজ, কিন্তু তা করতে গিয়ে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া কিংবা বৈরী অবস্থান তৈরি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।
ইন্টারনেট সূত্রে জানা যায়, খ্রিস্টধর্ম প্রচারে অতি-উৎসাহী কিছু চার্চ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মাত্র ৫ হাজার জনসংখ্যার কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেলেই তাকে টার্গেট করে কাজ শুরু করে। প্রথমে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক কাঠামো, ভাষা, জীবনপ্রণালী ইত্যাদি ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয়। তারপর তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রকল্প। পশ্চিমা জগতের কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্রের সাথে নব্যশক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ তাদের রাজনৈতিক-সামরিক ও কৌশলগত স্বার্থের সহযোগী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। শুরুতে দান-দক্ষিণা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে সখ্য এবং নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা হয়। এভাবে টার্গেট জনগোষ্ঠীর কাছে তারা হয়ে ওঠেন ত্রাণকর্তা। অতঃপর চলতে থাকে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকে তার পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া। তাদের বোঝানো হয়, পারিপার্শ্বিক জনগোষ্ঠীর শোষণ ও অবহেলার কারণেই তারা পিছিয়ে আছে। এ কাজে হাতের কাছে পাওয়া যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কিছু সুবিধাভোগী মানুষ। যারা নিজ নিজ এনজিও কার্যক্রমে উদার সহযোগিতার বিনিময়ে পুঁজিবাদের বিশ্ব বিজয়ের এই সুদূরপ্রসারী নবঅভিযানে পথপ্রদর্শক ও ‘লোকাল কোলাবরেটর’-এর ভূমিকা পালন করেন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। কিছু রাজনৈতিক দল-উপদলকেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিপরীতে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থক সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। তারা কথিত ‘আদিবাসী’ সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হতে গিয়ে এমন সব কথা বলেন বা কাজ করেন, যা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থের জন্য সংকট সৃষ্টি করে।
এর পরবর্তী ধাপে শুরু হয় ধর্মান্তরকরণ। এভাবেই মিজো, নাগা, গারো, খাসিয়া, বোড়ো, টিপরা সম্প্রদায়সহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব ক্ষুদ্র জাতি-উপজাতি আজ খ্রিস্টধর্মের বলয়ে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই ধারায় কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ইন্টারনেটে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট চালু রয়েছে বহুকাল ধরে। এগুলোতে যে ধরনের প্রচার-প্রচারণা করা হয় তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকার, রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ বা প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় না।
‘আদিবাসী’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে- একটি অঞ্চলে সুপ্রাচীন অতীত থেকে বাস করছে এমন জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র জাতি-উপজাতি হলেই ‘আদিবাসী’ বা আদি-বাসিন্দা হবে তেমন কোন কথা নেই। আদিবাসী হলো ঐসব জনগোষ্ঠী যারা কোনো একটি বিশেষ এলাকায় জন্ম-জন্মান্তর থেকে অবস্থান করছে, যারা ‘ভূমি সন্তান’ হিসেবে পরিচিত। পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত পাহাড়ীদের আদিনিবাস এখানে নয়। তারা মঙ্গোলয়েড বংশোদ্ভূত এবং বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার)-এর আরাকান, ভারতের বিহার ও মিজোরাম, থাইল্যান্ড ও চীন হতে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে। ‘আদিবাসী’র আভিধানিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। ‘আদিবাসী’ মানে হলো ‘ভূমি সন্তান’। ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত ইংলিশ-বাংলা অভিধানে অইঙজওএওঘঅখ বলতে ঐসব মানুষ এবং প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে যারা আদিকাল থেকে একই স্থানে বসবাস করছেন এবং পরিচিতি পেয়েছেন।
অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিজির দিকে তাকালে আসল আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। সেখানে বসবাসকারী স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী যারা ভূমি সন্তান হিসেবে পরিচিত। তারা কোনো অঞ্চল থেকে গিয়ে উক্ত এলাকায় বসতি স্থাপন করেনি এবং তাদের সংস্কৃতি এবং আচারের উৎসও তাদের নিজস্ব। তারাই হলো আসল আদিবাসী। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান্স, অস্ট্রেলিয়ার এবরিজিন্স। উক্ত জনগোষ্ঠী ইউরোপিয়ান কর্তৃক আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্ব থেকেই ঐ দেশে বসবাস করতো।
বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিম-লে ‘আদিবাসী’ বা আদি-বাসিন্দাদের উত্তরসূরি হওয়ার প্রথম দাবিদার এদেশের কৃষক সম্প্রদায়, যারা বংশপরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী মাটি কামড়ে পড়ে আছে। বানভাসি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নদীভাঙন, ভিনদেশী হামলা- কোন কিছুই তাদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। নদীভাঙনে কেবল এখান থেকে ওখানে, নদীর এক তীর থেকে অপর তীরে সরে গেছে। এ মাটিতেই মিশে আছে তাদের শত পুরুষের রক্ত, কয়েক হাজার বছরের। কাজেই বাংলার ‘আদিবাসী’ অভিধার প্রকৃত দাবিদার বাংলার কৃষক- আদিতে প্রকৃতি পূজারী, পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার এই বদ্বীপ ভূমিতে আদি-অস্ট্রিক, অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, মোংগল, টিবেটো-বার্মান- বিচিত্র রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের আগে। অতঃপর ধাপে ধাপে এসেছে ‘শক-হুনদল পাঠান-মোগল’, সেই সঙ্গে ইরানি-তুরানি-আরব। সবশেষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আমলে স্বল্পমাত্রায় হলেও পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ, ফরাসি, গ্রিক। কালের প্রবাহে বিচিত্র রক্তধারা একাকার হয়ে উদ্ভূত হয় এক অতি-শংকর মানবপ্রজাতি-‘বাঙালি’। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত জাতি-উপজাতি আজকের দিনেও তাদের পৃথক সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করছে।
ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এতদঞ্চলে আগমন কয়েকশ’ বছরের বেশি আগে নয়। বিশেষ করে চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের এতদঞ্চলে আগমনের নানা বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাসে বিধৃত আছে। চাকমাদের এতদঞ্চলে আগমন তিন-চারশ’ বছর আগে। থাইল্যান্ড বা মিয়ানমারের কোন একটি অঞ্চলে গোত্রীয় সংঘাতের জের ধরে এই জনগোষ্ঠী আরাকান থেকে কক্সবাজার এলাকা হয়ে চট্টগ্রামে আগমন করে এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে বাস করতে থাকে। এক সময়ে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাজশক্তিতেও পরিণত হয়েছিল। এ জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয় ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা লুসাই পাহাড়ে তাদের দখল স্থাপনের জন্য হামলা চালানোর সময় চাকমা সম্প্রদায়কে কাজে লাগায়। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে মিজোদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে। তার বিনিময়ে লড়াই শেষে তাদের রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বসতি গড়ার সুযোগ দেয়া হয়। মারমা সম্প্রদায়ের ইতিহাসও প্রায় একই রকম।
সম্প্রতি বান্দরবানের বর্ষীয়ান মং রাজা অংশে প্রু চৌধুরী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা এই অঞ্চলে আদিবাসী নই’। বান্দরবান এলাকায় মারমা বসতি ২০০ বছরেরও পুরনো। মং রাজাদের বংশলতিকা এবং ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী ‘ত্রিপুরা’। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। কথিত আছে সেখানকার রাজরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতর অংশ স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়ে এখানে এসেছে। সেটাও বেশিদিনের কথা নয়। এর বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে আরও ৮টি ক্ষুদ্র জাতি। তাদের কোন কোনটি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদেরও পূর্ব থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের পৃথক নৃ-তাত্ত্বিক সত্তা দৃশ্যমান। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওরাঁও, রাজবংশী, মনিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই বৃহত্তর অংশ রয়েছে প্রতিবেশী ভারতে। ক্ষুদ্রতর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আগে-পরে বাংলাদেশে এসেছে। তারাও দীর্ঘকাল ধরে এদেশে বসবাস করছে বিধায় এদেশের নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার ও সমসুযোগ তাদের অবশ্য প্রাপ্য। তবে এদের কোনটিই বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা বা ‘আদিবাসী’ নয়।
বাংলাদেশে আদিবাসী কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি; বরং বাংলা ভাষাভাষীরাই এদেশের আদিনিবাসী। আর পার্বত্য এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিরা জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এদেশে তথা ভারতবর্ষে এসেছে এবং উপজাতীয়দের সংস্কৃতি ও আচারের উৎস এ অঞ্চলের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচারের উৎস তারা যেসব অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখান থেকেই আসা। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে কেবল ক্ষুদ্র উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। কোনোভাবেই তাদেরকে আদিবাসী বলা বা আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা সমীচীন নয়।
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১৩টি উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস, তাদের আগমন হয় ১৬০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। তাদের প্রত্যেকের আদিনিবাস এবং পার্বত্য জেলায় আগমনের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত মগ বা মার্মা, মুরং, ত্রিপুরা, লসাই, খুমিস, বোমাং বা বম, খিয়াং, চাক, পাঙ্খু, তঞ্চক্ষা, কুকি, রাখাইন, চাকমাসহ সকল উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও দেশ থেকে এসে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ফলে উপরিউক্ত জাতি-গোষ্ঠীর অতীত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত পাহাড়িরা কখনোই এ এলাকার আদিবাসী নয়।
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পাহাড়ি এবং আদিবাসীদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারার কথা নয়। দেশের সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠীর একটি অংশ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে পাহাড়িদেরকে আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। এ কাজে কিছু দেশী-বিদেশী এনজিও জড়িত, যারা তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত পাহাড়িদের দৈন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নের নামে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। এতে সাধারণ পাহাড়িদের কাছ থেকে তারা প্রচুর সাড়াও পাচ্ছে। আর এভাবে একবার যদি তারা উপজাতিদেরকে আদিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের জন্য তা হবে চরম শঙ্কার কারণ। কেননা আদিবাসীদের বিষয়ে জাতিসংঘের নীতিমালা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং স্পর্শকাতর।
আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইএলও কনভেনশন ১০৭ যা বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে, একই সাথে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ (১৯৮৯) এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি রেজুলেশন পাস করে; যা বাংলাদেশ সরকার সঙ্গতকারণেই অনুমোদন করেনি। কারণ এ সকল রেজুলেশনে অনেক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো দ্বারা আদিবাসীদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের নির্দেশনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উক্ত রেজুলেশন প্রযোজ্য নয়। কারণ বাংলাদেশে আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের একাংশে বসবাসকারী ঐ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত। তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পৃথক জাতিসত্তার অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ সামগ্রিক জাতীয় পরিচয়ে তাতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। মনে রাখতে হবে যে, তারাও এই স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশেরই নাগরিক। তাই দেশের অন্যান্য স্থানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রেখে ঐ অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নেও আমাদেরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনোভাবেই যাতে তাদের নাগরিক অধিকার বিঘ্নিত না হয়। কেননা, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং মানবিক।
একটি আধুনিক জাতির রাষ্ট্র যতই এগিয়ে যাবে তার পরিমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কালপ্রবাহে বৃহত্তর দৈশিক আবহে ততই একক ও অভিন্ন পরিচয়ে ধাতস্থ হয়ে যাবে। এটাই ইতিহাসের ধারা। দুনিয়াজুড়ে প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিরাজমান। এক হিসেবে পৃথিবীতে এখনও এরকম ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি মেনে নিয়েই তাদের আয়ত্ব করে নিতে উদ্যোগী হতে হবে সব জাতি-রাষ্ট্রকে। সেজন্য প্রয়োজন উদার ও সংবেদনশীল মানসিকতা। পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা। তাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থান থেকে অতিদ্রুত সামগ্রিক জাতীয় পরিমণ্ডলে অন্যদের সমকক্ষতায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা। পশ্চিমা বিশ্ব এখানেই বাদ সাধছে। একদিকে দুনিয়াজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘নোডাল পয়েন্ট’ গুলোতে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে চলছে বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে পশ্চিমা জগতের ‘আউটপোস্টে’ পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতি-রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে তাদের পৃথক করে দুনিয়াজুড়ে পশ্চিমাদের কায়েমি স্বার্থের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ‘আদিবাসী’ স্লোগান এক্ষেত্রে কেবল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। চুক্তির ফলে একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সন্ত্রাসীর অস্ত্র সমর্পণ নিশ্চিত করা যায়নি। অপরদিকে ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সংস্কারপন্থী) নামে নতুন সশস্ত্র সংগঠনের জন্ম হয়েছে। চুক্তির ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের যুদ্ধ হ্রাস পেলেও সাধারণ মানুষ হত্যা হ্রাস করা যায়নি। বরং সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রত্যাবাসিত বাঙালিরা শরণার্থীর মতো নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী নিরাপত্তাবাহিনী প্রত্যাহার করায় দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারী নিরীহ উপজাতীয়দের নিরাপত্তা সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ভূখ-কে ব্যবহার করছে।
প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী জেএসএস ও ইউপিডিএফ’র সন্ত্রাসী সদস্য এবং কিছু কুমতলববাজ এনজিও কর্মী। এর বাইরে পাহাড়ের সকল শ্রেণীর বাঙালি ও উপজাতীয় বাসিন্দাগণ শান্তিপ্রিয় ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। স্বাধীন জুম্ম ল্যান্ড, সেনা প্রত্যাহার, বাঙালি খেদাও কোনো কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। বরং বর্তমানে বাঙালি-পাহাড়ী সহাবস্থান, সৌহার্দ্য, সৌজন্যতা, আতিথেয়তা এমনকি বিয়ে-শাদীর মতো আত্মীয়তা ও সামাজিক সর্ম্পক বিনিময় হচ্ছে। আবহমান কাল হতে বিরাজমান এই সহজ, সুন্দর, স্থায়ী শান্তির সম্পর্ক ও সহাবস্থানকে বর্তমান ও সাবেক গুটিকয়েক সন্ত্রাসী এবং অন্যদিকে শান্তিচুক্তির ছায়ায় ইউএনডিপির মতো বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর বিতর্কিত কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত করছে।
লেখক : সমাজকর্মী, বিশ্লেষক ও গবেষক